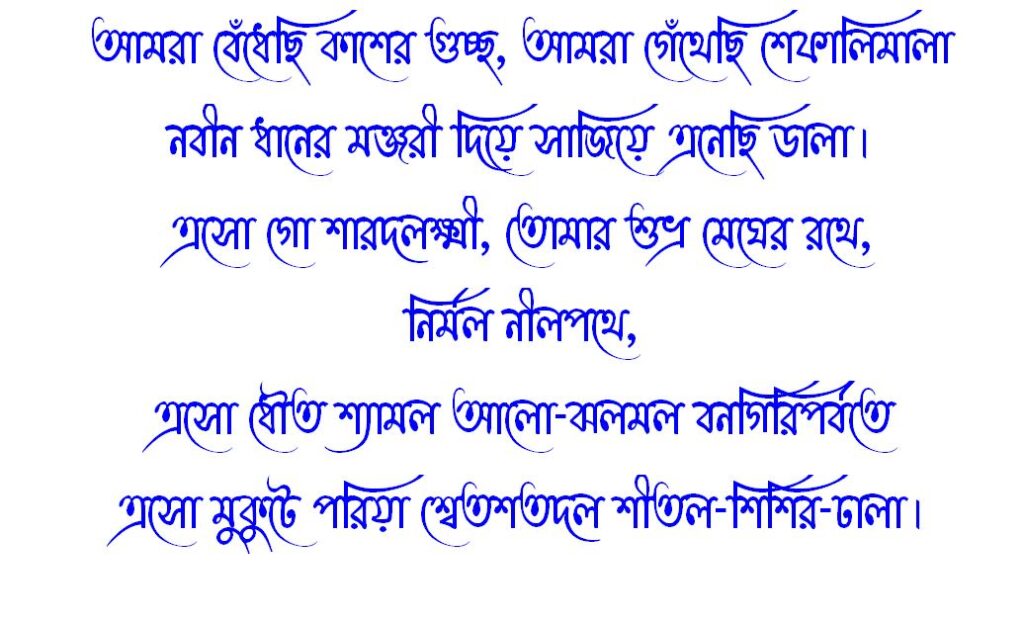

বর্ষা-মেঘের আঁচল খসিয়ে যখন শরৎঋতু আমাদের দোরগোড়ায় উঁকি দেয়, তখন আশ্বিনের শারদপ্রাতে আপামর বাঙালির মন উন্মন হয়ে ওঠে মা দুর্গার মর্ত-আগমনে। দুর্গাপূজা বাঙালির বৃহত্তম আনন্দযজ্ঞ, অন্যতম সামাজিক মিলন-অনুষ্ঠান। যে দুর্গাপূজাকে ঘিরে উচ্ছাস আর উন্মাদনা উৎসবের দিনগুলিতে প্রত্যেক বাঙালিকে নেশাগ্রস্ত করে রাখে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তার প্রভাব কেমন ছিল তা জানতে আমরা অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকি। ঠাকুরবাড়ি ছিল ব্রাহ্ম অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। সেখানে দুর্গাপূজার মতো সাকার ঈশ্বর সাধনা কিভাবে পালিত হত? কে শুরু করেছিলেন এই পরিবারে পূজা আর সেটা বন্ধই বা হল কীভাবে?
১৭৮৪ সালে ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরের দুই নাতি, নীলমণি এবং দর্পনারায়ণের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নীলমণি কুলদেবতা লক্ষীজনার্দনশিলাকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে গৃহত্যাগ করে কলকাতার মেছুয়াবাজার অর্থাৎ আজকের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ‘জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি’ পত্তন করেছিলেন। সেই বাড়িতেই, নীলমণি ঠাকুরের উদ্দ্যোগে সূচনা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা।
নীলমণির আর্থিক অবস্থার কারণে তাঁর আমলের পূজা ছিল আড়ম্বরহীন, সাদামাটা। কিন্তু সেই পূজাই তাঁর বংশধর, অতুল বৈভবের অধিকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাত ধরেই রাজকীয় আকার ধারণ করেছিল।

দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা সেই সময় অন্য ধনী পরিবারগুলির কাছে রীতিমতো ঈর্ষার কারণ ছিল। পুজোর আগে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হত শঙ্খচিল, মা দুর্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য। বিজয়া দশমীর দিন সকালবেলা উড়িয়ে দেওয়া হত নীলকণ্ঠ পাখি, মহাদেবকে খবর দেবে বলে।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যেত পূজোর অনেক আগে থেকেই। সমস্ত সাত্ত্বিকতা মেনে প্রতিমা গড়ার মাটি আসত গঙ্গার পাড় থেকে। গরুর গাড়িতে করে দেবীর চালচিত্র আসতো ঠাকুরবাড়িতে। শিল্পীর নিপুন হাতের কারিকুরিতে ধীরে ধীরে সেজে উঠত একচালার কাঠামোয় সপরিবারে দেবী দুর্গা, পায়ের তলায় দেবীর বাহন সিংহ আর মহাবিক্রমশালী অসুর। খড়ের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ পড়া শুরু হলেই ছোট ছোট ছেলেরা পাঠশালা পালিয়ে ঠাকুরদালানে গিয়ে ভিড় জমাত, ঠাকুরগড়া দেখবার জন্য।
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিমার টানা টানা চোখ সবার নজর কাড়ত। দ্বারকানাথের স্ত্রী, অসামান্যা সুন্দরী দিগম্বরী দেবীর মুখের আদলে গড়া হত দেবী দুর্গার মুখ। দেবীর অঙ্গে থাকতো বহুমূল্য অলংকার, সোনার গয়না, মাথায় সোনার মুকুট, কোমরে চন্দ্রহার। পরনে বেনারসি কিম্বা গরদের শাড়ি। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘প্রথমে খড়ের কাঠামো, তার উপরে মাটি, খড়ির প্রলেপ, তার উপরে রং , ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুঁটিনাটি আর সমস্ত কার্য, সর্বশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের উপর দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক, দেবসভা উদঘাটিত হত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডল, বসনভূষণ ,সাজসজ্জা প্রস্তুত হত আমাদের বড়ই কৌতূহল হত। অর্ধচন্দ্রাকৃতির একচালার মূর্তিই ছিল ঠাকুরবাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য। তবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত প্রতিমার মুখের আদলের ওপর।’
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজায় মায়ের ভোগ ছিল দেখার মতো। দু’বেলায় সব মিলিয়ে একান্ন রকমের পদ মায়ের ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হত, সাথে থাকত ফল, ডাবের জল ইত্যাদি। পরে সেগুলো পুজোর দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হত। সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে আরতি দেখতেন। রুপোর প্রদীপদানিতে একহাজার ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে, রুপোর ঘন্টা বাজিয়ে শুরু হতো আরতি। সেই প্রদীপ জ্বলত তিনদিন, তিনরাত্তির ধরে। পশুবলির পরিবর্তে দেওয়া হত কুমড়ো বলি।
তখনকার সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষের বাডিতেই দুর্গাপূজার আয়োজন করা হত। কার পূজো কত জমকালো আর আকর্ষণীয় তা নিয়ে চলত সুস্থ প্রতিযোগীতা। অনিবার্যভাবেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পূজোর উপরে কেউই টেক্কা দিতে পারতেন না। তবে সকলেই ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসবে আমন্ত্রণ পেতেন। আমন্ত্রণপত্র লেখা হত দ্বারকানাথের পিতা রামমণি ঠাকুরের নামে।
শোনা যায়, একবার পিতামহের সেই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে বারো বছর বয়সের বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করতে, রামমোহনকে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘সামনে পুজো তাই তিনদিনই প্রতিমাদর্শনে আপনার নিমন্ত্রণ, পত্রে দাদুর এই অনুরোধ।’ রামমোহন রায় এই আমন্ত্রণে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মূর্তি পূজার বিরোধী। নিমন্ত্রণপত্রটি প্রত্যাখ্যান করেননি আবার সরাসরি সেটা গ্রহণও করেননি, তিনি তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদের কাছে দেবেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে, পিতার হয়ে সেটা গ্রহণ করে কিশোর দেবেন্দ্রকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন।
দ্বারকানাথ ঠাকুর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাড়ির ছেলেমেয়ে, গৃহবধূ আর আত্মীয়স্বজনকে দামী দামী পোশাক উপহার দিতেন। পুজোর আগে থেকেই দর্জিদের সেলাই মেশিনের শব্দে ঠাকুরবাড়ি মুখরিত হয়ে থাকত। দিনরাত এক করে তারা বানাতেন সকলের পুজোর পোশাক। ছেলেদের জন্য জরির টুপি, চাপকান, ইজার এবং মেয়ে বউদের জন্য পছন্দমত জামাকাপড় সাথে নানা কাজ করা রেশমি রুমাল। পুজোর জন্য ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেক মেয়ে-বউ দ্বারকানাথের কাছ থেকে উপহার পেতেন এক শিশি দামী সুগন্ধী, খোপায় দেওয়ার সোনারুপোর ফুল, কাঁচের চুড়ি আর নতুন বই। বাড়ির দুর্গাপুজোয় ছোট থেকে বড়, মেয়ে-বউ এমনকি বাড়ির ভৃত্য-কর্মচারীরাও পেতেন নানান শৌখিন উপহার।

ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনও ছিল দেখবার মত রাজকীয়। দশমীর আরতির পরে ঢাকঢোল, কাঁসরঘণ্টা আর গ্যাসবাতি নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত গঙ্গার ঘাটের দিকে। পুরুষেরা নতুন পোশাক পরে প্রতিমা ভাসানে যেতেন, সাথে যেত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে প্রহরী। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা থাকতেন তেতলার ছাদে। সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথায়, ‘বিজয়ার দিন ছাদে ওঠা তাঁদের একটুকরো মুক্তি ছিল’।
দ্বারকানাথের নির্দেশে, সম্ভবত তাঁর বৈভব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, বিসর্জনের আগে প্রতিমার শরীর থেকে বহুমূল্য সোনার গয়নাগুলি খুলে নেওয়া হত না। সেগুলো সমেতই প্রতিমাকে ভাসিয়ে দেওয়া হত গঙ্গাবক্ষে। পরে নৌকোর মাঝি বা অন্যান্য কর্মচারীরা জল থেকে তুলে নিতেন সেই গয়নাগুলি। সেসব আর কখনোই ঠাকুরবাড়িতে ফিরে যেত না, বনেদিয়ানার আভিজাত্যে দ্বারকানাথ সেই গয়না গ্রহণ করতেন না !
বিজয়ার দিন মিষ্টিমুখ আর কোলাকুলির প্রচলন ছিল ঠাকুরবাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘বিজয়া তাঁদের জন্য খুব আনন্দের দিন ছিল। সেদিনও কিছু পার্বণী পাওয়া যেত। ঠাকুরবাড়ির যত কর্মচারী ছিলেন সবার সঙ্গে তাঁরা কোলাকুলি করতেন। বুড়ো চাকররাও এসে ঠাকুরবাড়ির ছোট-বড় সবাইকে প্রণাম করত।’
একালের মতো দুর্গাপুজোর পর ঠাকুরবাড়িতেও আয়োজন করা হত বিজয়া সম্মেলনী। বসত বিশাল জলসার আসর। ঠাকুরদালানের খোলা মঞ্চে ব্যবস্থা থাকত নাচগান, যাত্রা, নাটক সমেত নানা আমোদপ্রমোদেরও। সেকালের নামকরা ওস্তাদেরা তানপুরা নিয়ে এসে গানে গানে আসর মাত করে দিতেন। রাজকীয় ঝাড়বাতির নীচে চলত বিজয়ার রাজসিক খাওয়াদাওয়া- মিষ্টিমুখ, গোলাপজল, আতর, পান আর কোলাকুলি।

এরপর দ্রুত পট পরিবর্তন। ১৮৪৩ সালে দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর ঠাকুরবাড়িতে দূর্গাপূজা সমেত সব ধরণের মূর্তিপূজা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিরাকার ঈশ্বরচেতনা আর আদর্শই ছিল এর প্রধান কারণ। মহর্ষি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করলেও ঠাকুরবাড়ির অন্য সদস্যরা পুজো বন্ধের ব্যাপারে সকলে একমত ছিলেন না। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘দুর্গোৎসব আমাদের সমাজের বন্ধন, সকলের সাথে মিলনের এক প্রশস্ত উপায়। ইহার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে।’ এরপরও দু’তিন বছর ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা হয়েছিল কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেও অনুষ্ঠানে আর অংশগ্রহণ করতেন না। সেই সময় তিনি চলে যেতেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নতুবা তাঁর প্রিয়স্থান হিমালয়ে। এই ঘটনার অভিঘাতে জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী ঠাকুর পরিবার ভেঙে দু’টুকরো হয়ে গিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ পিতার আদর্শে জীবনে কোনো দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু তাঁর বিপুল সাহিত্যভান্ডারে দুর্গাপূজার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে কবিতা, ছোটগল্প, নাটক কিংবা উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে। আসলে শরৎ ঋতুর এই উৎসবকে তিনি মাটির প্রতিমা-বন্দনায় মৃন্ময়ী না করে শরতের অমল আলোয় প্রকৃতি বন্দনা করে তাকে চিন্ময়ী করে তুলেছেন। তাই তো তিনি গেয়েছেন-
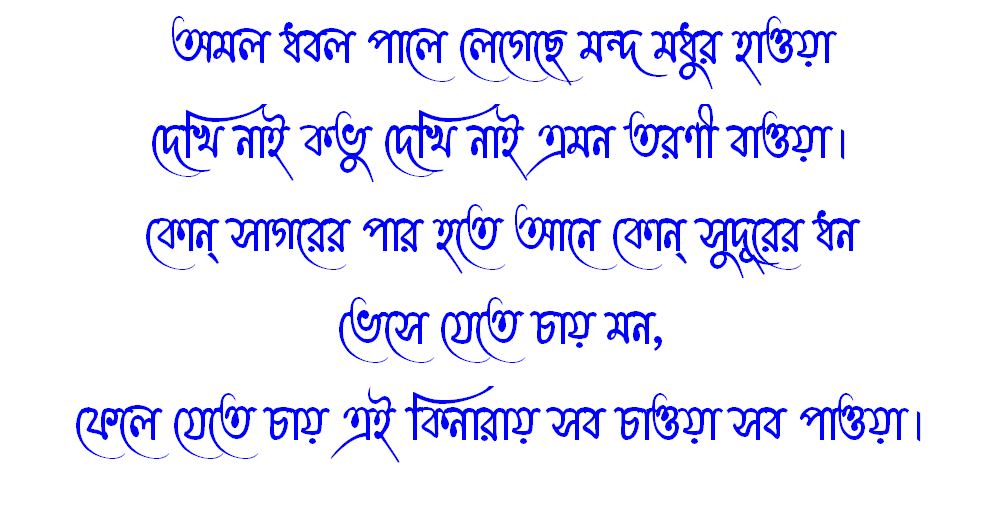

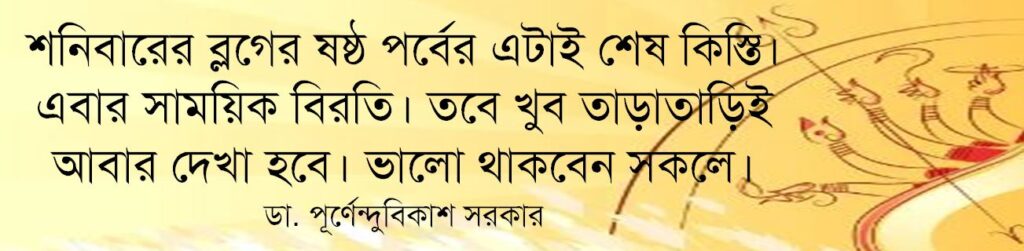
আপনাকেও শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনার মূল্যবান লেখাগুলি এখন কয়েক সপ্তাহ পাব না ভেবে খারাপ লাগছে। সপরিবারে ভালো থাকুন। আনন্দে আপনাদের পূজা সার্থক হোক।
যথাশীঘ্র আপনার ব্লগে ফিরে আসুন। নমস্কার।