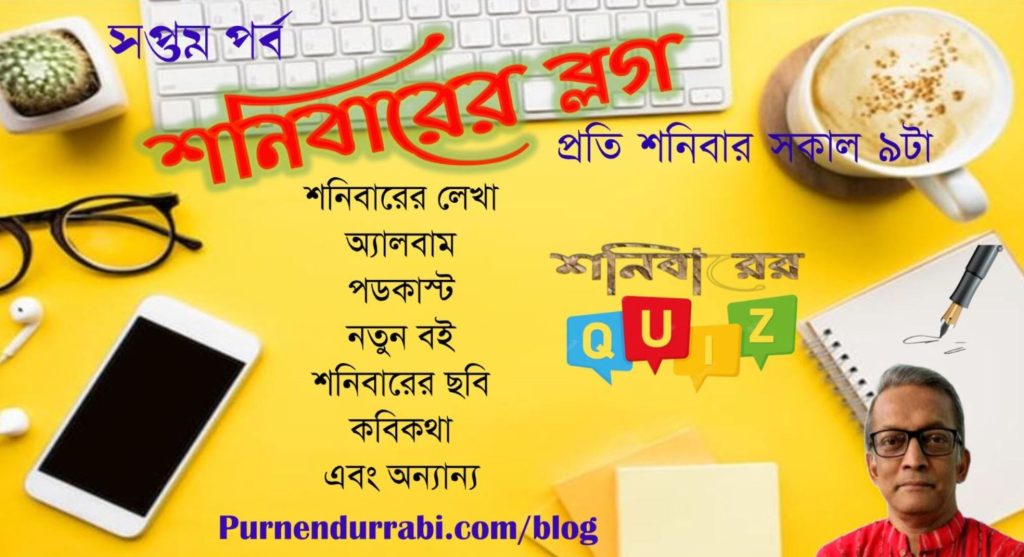

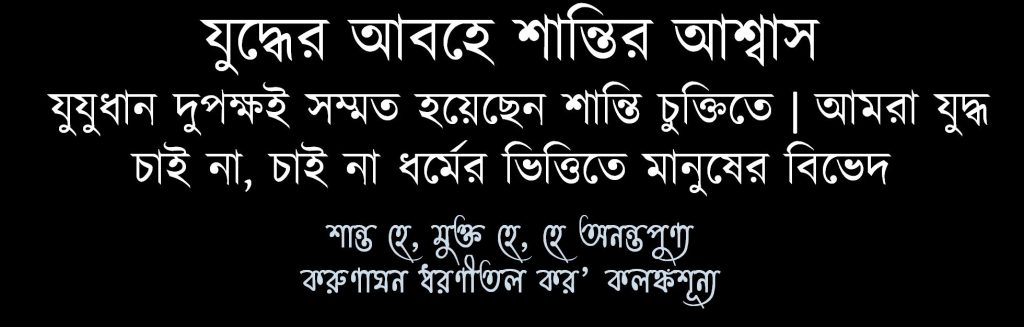
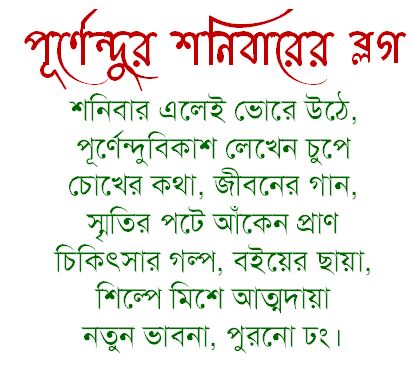

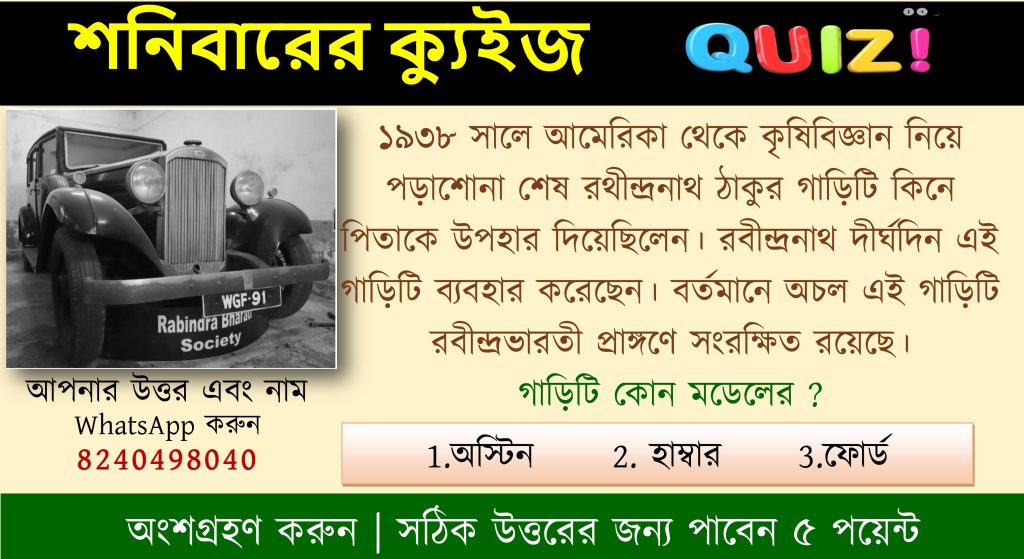
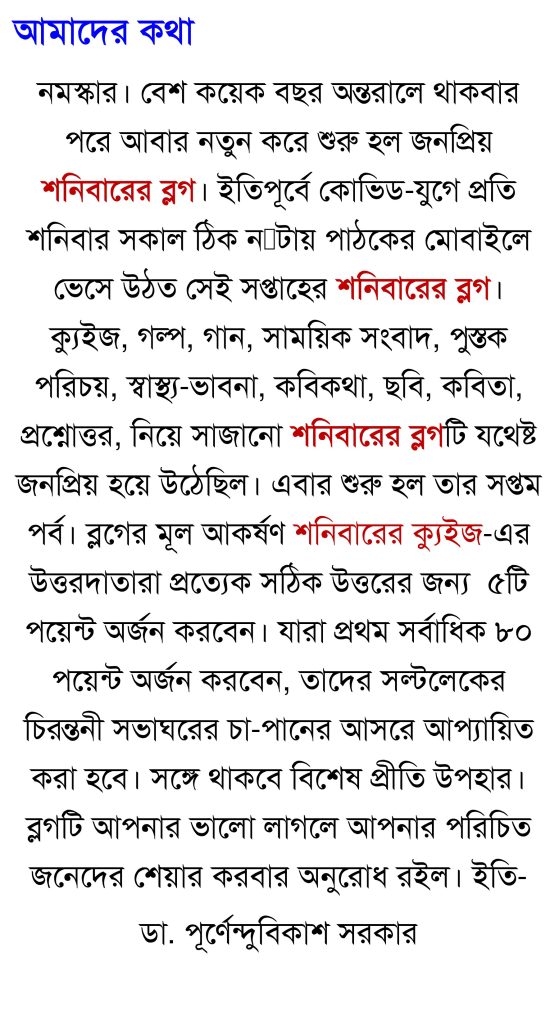


অজানার পথে
১৭৮৪ সাল। গ্রীষ্মের এক ভয়ংকর দুপুর। আকাশে একটুকরো মেঘ নেই। সূর্য যেন তার সমস্ত তেজ দিয়ে পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চাইছে। বাতাসে আগুনের ছটা। পাখি-পাখালিরা গাছের ঘন ডালপালার আড়লে নিজেদের লুকিয়ে রাখবার ব্যার্থ চেষ্টায় দিশাহারা, নিশ্চুপ। রাখালের বাঁশির সুর কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে! গবাদি পশুদের চারণভূমি আজ যেন তপ্ত মরুভূমি। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কুকুরগুলো লম্বা জিভ বের করে হাঁপিয়ে সারা। সেই দুঃসহ দুপুরে, আঁকাবাঁকা খানাখন্দে ভরা কাঁচা পথ ধরে ক্লান্ত পায়ে হঁটে চলেছেন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। দুচোখে কেবল হতাশা আর শূন্যতা। নিজের ভাইয়ের কাছে প্রতারিত হয়ে, অনেক অভিমানে ঘর ছেড়ে চলেছেন অজানার পথে, একবস্ত্রে। সঙ্গে পুত্র-পরিবার আর গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন। যে ঘর ছেড়ে আজ তিনি অনিশ্চিয়তার পথে নেমেছেন, সে ঘর নির্মাণের পিছনে রয়েছে নিজের কঠোর পরিশ্রম আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক কষ্টে আয় করা অর্থ। শুধু ঘরই নয় ফেলে এসেছেন সারাজীবনের সঞ্চয় আর আত্মীয়জনেদের। জানেন না সন্তানদের নিয়ে কোথায় রাত্রিযাপন করবেন, আহারেরই বা কি হবে। সামনে শুধুই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কালো অন্ধকার। বেলা পড়ে আসছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর যাত্রীদের হঠাৎ চোখের পড়ল টলটলে জলে ভরা পুকুরঘাট আর পাশের ছায়াঘেরা তেঁতুল গাছটার দিকে। যেন ভগবান মরূদ্যান সাজিয়ে রেখেছেন পথক্লান্ত পথিকদের জন্য। ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় সকলে আশ্রয় নিলেন সেই ছায়াতলে। পুজা করলেন গৃহদেবতার, সামান্য কিছু আহারের পরে চোখে নেমে এল তন্দ্রার ঘোর।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ভারতীয় ঐতিহ্য, স্থাপত্য আর সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই বাড়ির বাসিন্দারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মূল্যবান কিছু অংশ, এবং মহানির্বাণ সমাপ্ত হয়েছিল এই বাড়িতেই, যা পৃথিবীর মানচিত্রে জোড়াসাঁকো বাড়িটিকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, ঠাকুর-পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যের নানাবিধ প্রতিভার উদ্ভাসে ভাস্বর হয়ে রয়েছে জোড়াসঁকোর ঠাকুরবাড়ি। বর্তমানে ভারত সরকার বাড়িটিকে হেরিটজ-ভবন’এর স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। উত্তর কলকাতার চিৎপুর সংলগ্ন প্রায় পঁইত্রিশ হাজার বর্গমিটার জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর অবস্থান। তবে প্রথমে শুরু হয়েছিল মাত্র এক বিঘে জমির উপরে নির্মিত ছোট্টো একটা ঘর দিয়ে। আর সেই ইতিহাসও অত্যন্ত চমকপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি তার খোলনোলচে বদলিয়ে এক যুগান্তকারী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন করে মেলে ধরেছিল। সেই ঊষালগ্নের প্রদীপ যিনি জ্বালিয়েছিলেন, সূচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক নবজাগরণের ইতিহাস, তিনি ঠাকুর বংশের পুর্বপুরুষ নীলমণি ঠাকুর, এই বিশাল স্থাপত্যের মূল কারিগর। তাঁর ‘একবিঘে জমির ছোট্টো নির্মাণ’টি ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে, অজস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। রেনেসাঁর সেই সন্ধিক্ষণে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়িটির জৌলুস আর আভিজাত্য সূর্যের আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। চিৎপুরের সীমানা অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিল শহরের কোনায় কোনায়, ভারতের নানা প্রান্তে এমনকি বিদেশের মাটিতেও। ব্যবসায়িক সাফল্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যচর্চা, শিল্পকলা, দার্শনিকতা ইত্যাদি বহুবিধ বৈচিত্রের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল এই বাড়িতেই। কিন্তু কালের নিয়মে ধীরে ধীরে সেই সুদিনেও ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। মানুষের ভীড়, কোলাহল, স্বার্থপরতা আর কূটকাচালীতে ধীরে ধীরে সেই গৌরবের দিনগুলিতে নেমে এসেছিল অবক্ষয়ের অন্ধকার।
নতুন জনপদ
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বাংলার শাসনভার পাঠান সুলতান নাসির সাহেবের হাতে। নাসিরসাহেবেরর পুরো নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫-১৪৫৯)। শান্তিপ্রিয় নাসিরুদ্দিন সফলভাবে রাজত্ব করেছেন প্রায় তেইশ বছর ধরে। প্রজাদের সুখসুবিধার জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করে সুনামও কুড়িয়েছেন। তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় জেলাটির নাম যশোর। যশোর বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের ভৈরব নদীর কোল ঘেঁসে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক দু’দিক থেকেই এই অঞ্চলটির গুরুত্ব অসীম। এছাড়া অবাধ বানিজ্যকেন্দ্র হিসাবে যশোরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সমস্ত বণিকসমাজের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান যশোরকে ফুলের রাজধানী বলা হয় কেননা যশোরের গদখালি অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের ৮০% ফুল সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম ও প্রাচীন সেনানিবাস, সফটওয়্যার ও টেকনোলজি পার্ক, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি, বহু মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সমারোহে যশোর জেলাটি বাংলাদেশে বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছিল। যশোরের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ-পিপাসুদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। খুলনা থেকে কলকাতায় সহজে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর রোডটি নির্মাণ করেছিলেন। শোনা যায় খুলনার সম্ভ্রান্ত জমিদার কালী পোদ্দার তাঁর মায়ের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য এই বৃক্ষ-শোভিত মনোরম সড়কটি নির্মান করেছিলেন। যদিও বর্তমনে নানা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে যশোরসহ সমগ্র বাংলাদেশের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে।
যশোরের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাম চেঙ্গুটিয়া, খুবই সাদামাটা ছোটো একটি অনুন্নত গ্রাম। নিজের রাজত্বের পরিধি বৃদ্ধির জন্য নাসিরুদ্দিন তাঁর বিশ্বস্ত সভাসদ পীর আলিকে চেঙ্গুটিয়া পরগনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেখানে নতুন লোকালয় গড়ে তোলবার জন্য। পীর আলি কিন্তু তার প্রভুর মত সরল মনের মানুষ ছিলেন না। তাঁর নানান প্যাঁজ-পয়জারের জন্য প্রজাদের প্রায়ই অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হত। সুলতান নাসিরুদ্দিনের নির্দেশ পেয়ে, কিছুটা নিমরাজি হয়ে, লোকলস্কর নিয়ে পীর আলিকে কাজে নেমে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু একটা গোটা শহর গড়ে তোলা তো মুখের কথা নয়। এজন্য দরকার প্রচুর লোকজন, শ্রমিক, মালপত্র, সেগুলি রাখবার গুদামঘর আর উপযুক্ত পরিকল্পনা।
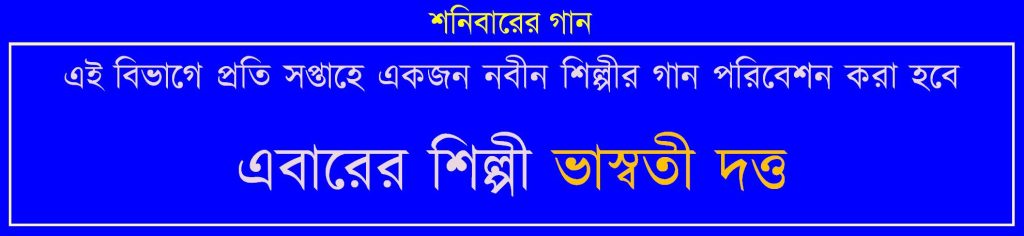

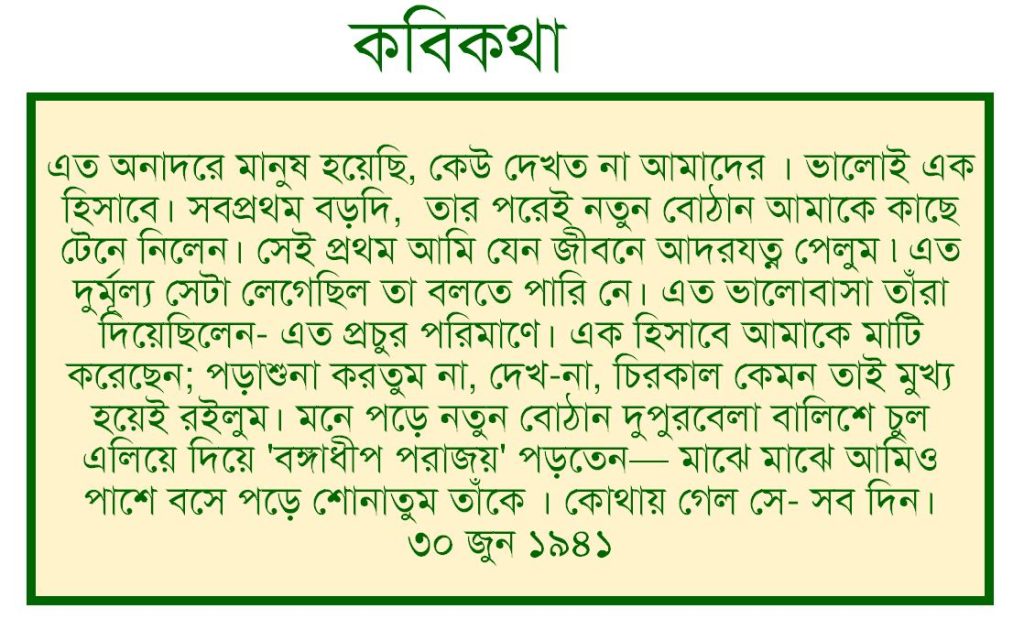
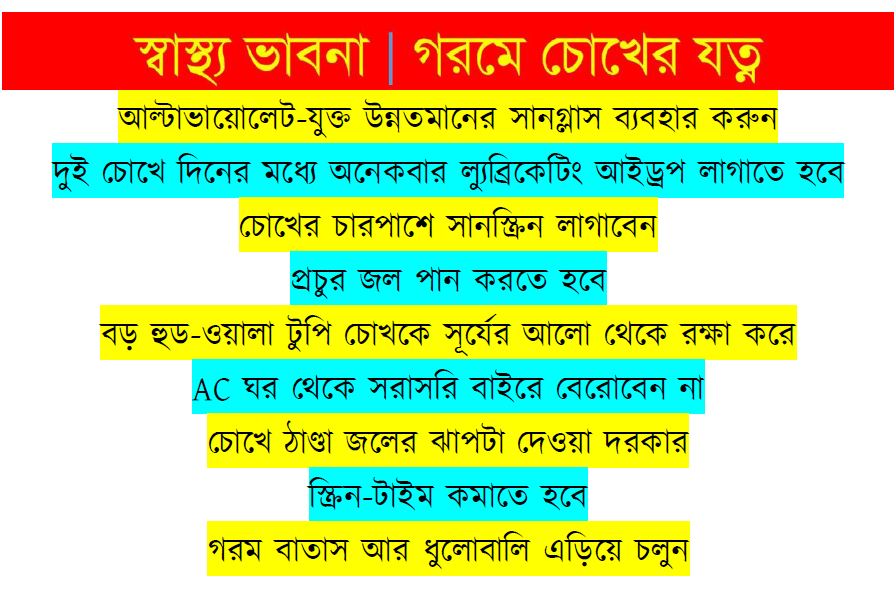
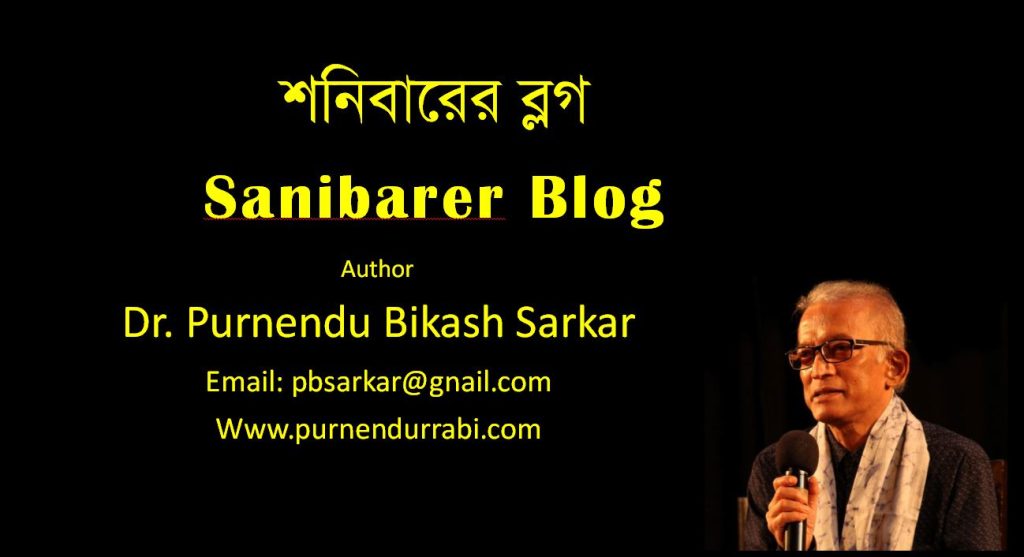
![]()