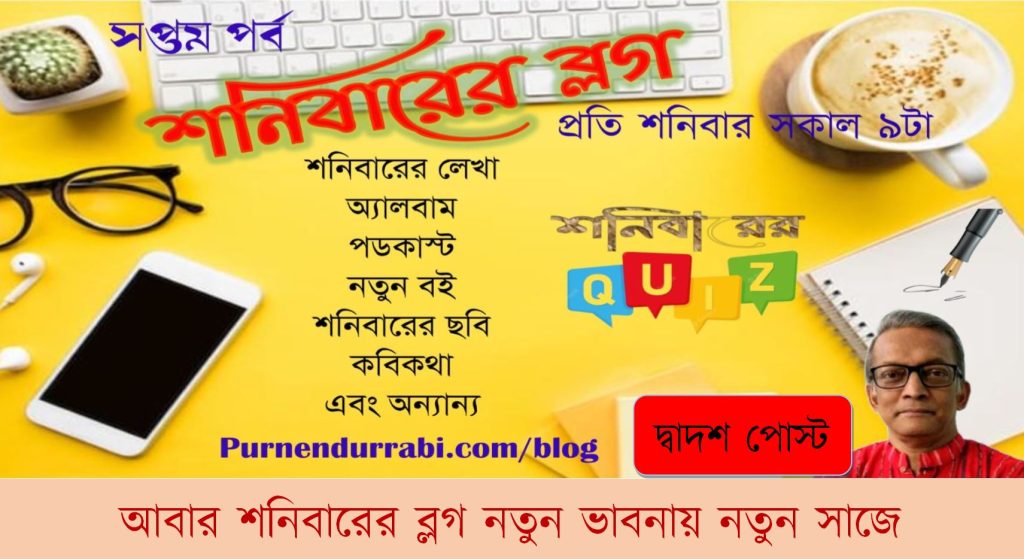

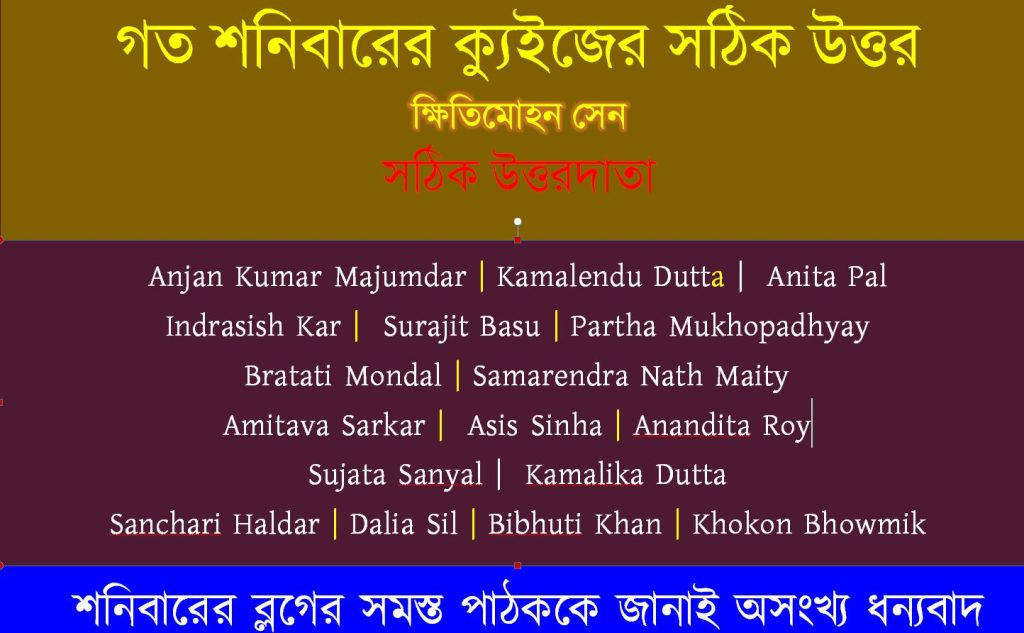
নমস্কার।
দেখতে দেখতে শনিবারের ব্লগ-এর সপ্তম পর্বের ১২টি পোস্ট সমাপ্ত হল। শনিবারের ব্লগের পাঠকদের উৎসাহ আর প্রশ্রয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আর মাত্র ৪টি পোস্ট। তারপর আমরা মুখোমুখি মিলিত হব চা আর গল্পের আড্ডায়। সাথে থাকবেন সব সময়। ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার
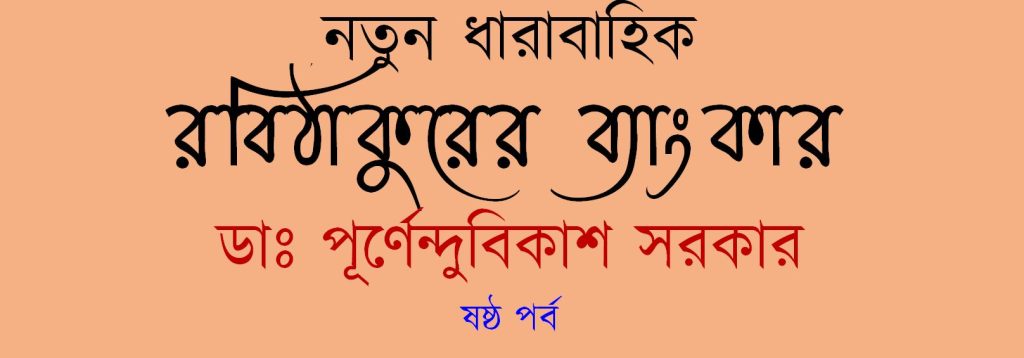
ষষ্ঠ পর্ব
বারেশো বিরানব্বই বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ মাসাধিককাল সোলাপুরে বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ‘বালক’ পত্রিকা সম্পাদনায় ব্যস্ত। আশ্বিন মাসে সম্পাদনের কাজ শেষ করে, একমাসের ছুটির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিয়েছিলেন উদ্দেশে কলকাতার ইট-কাঠ-চুন-সুরকির বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে সোলাপুর থেকে প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, ‘এখানে এসে অব্ধি এমনি ছুটির হাঙ্গামে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে । এখেনে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস—সমস্ত দিন একটা গড়িমসি ভাব—কখন লিখি বল ?… এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। এক্টা মহত্ত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্চে । মনে হচ্চে আমি নিষ্ফল । কি করব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে একটা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে।’ এই কর্মহীন অবকাশে, শরৎ-আকাশে রোদ-মেঘের খেলা আর উদার প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের পটভূমির আবহে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন অনেকগুলি সনেটধর্মী কবিতা। ১৮৮৩ সালে মৃণালিনীর সঙ্গে বিয়ে হলেও, জোড়াসাঁকোর হট্টমেলায় নববধুকে নিবিড়ভাবে কাছে পাওয়ার সুযোগ পাননি তরুণ রবি। সোলাপুরে এসে সেই আক্ষেপ পুরোপুরি মিটিয়ে নিয়েছিলেন নবীন দম্পতি। ততদিনে ঘরে এসেছে আর একটি নতুন প্রাণ, তাদের প্রথম সন্তান আদরের মাধুরীলতা। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ‘মনে হয়, কিশোরী বধূ মৃণালিনীকে দেহে-মনে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার আবেশ-বিহ্বলতা সনেটগুলির ভাবাবহ রচনা করেছে।’ (রবিজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ ১৯) বস্তুত সোলাপুরেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত মুক্তির স্বাদ উপভোগ করেছেন, ‘দেহ-মন নতুন সৃষ্টির কল্পনায় উদ্দীপিত’ হয়ে উঠেছিল।
জীবনের সত্তরটি বছরের পরেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। গোয়ার উপকূলবর্তী বন্দোরা শহরটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। অসীম বিস্তৃত সাগরের কলতান, উদার আকাশের প্রশান্তি আর নিঃশব্দ পরিবেশ বন্দোরাকে তাঁর এক মহৎ সাধন-আশ্রমে পরিণত করেছিল। সেখানেই তিনি নিজের অন্তর্জগতে আরাধ্য পরমেশ্বরকে গভীরভবে উপলব্ধি করতেন। কিন্তু ১২৯৩ বঙ্গাব্দে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন চুঁচুড়ায়, পরিবারের প্রিয়জনেদের কাছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার পাশে থেকে দিনরাত তাঁর সেবা করেছেন। ১৮৭৩ সালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের সময়, বালক রবি মহর্ষির প্রবল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের তাঁর মানসিক গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার অকপটে স্বীকার করেছেন, পিতার উপস্থিতি তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বোধকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে।
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে বারবার প্রকাশ পেয়েছে, কেবল সাহিত্যসৃষ্টি নয়—যত রকম আনন্দ, অভিজ্ঞতা কিংবা সাংস্কৃতিক পরিসরই হোক না কেন, তিনি প্রিয়জনকে সঙ্গী করতে চাইতেন। বিশেষত প্রিয়নাথ, যাঁকে তিনি শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নয়, একরকম সৃজন-সঙ্গী বলেও অনুভব করতেন। ১৮৮৬ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতার কোরিয়ান থিয়েটারে বিশ্বখ্যাত ইতালীয় বেহালাবাদক রেমিনির (Edward Reményi) অনুষ্ঠান ছিল। সে সময়ে কলকাতা ইউরোপীয় শিল্পীর আগমনে বেশ সরগরম। রবীন্দ্রনাথ নিজের আনন্দ-অভিজ্ঞতাকে কখনও একাকী ভোগ করতে চাননি। তাই প্রিয়নাথকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন, ‘যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেচেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুনলে চিরজীবন সার্থক হয় – এমন মধুর সঙ্গীত তাঁরা জন্মে কখনও শোনেন নি। আমি ছেলেদের নিয়ে আজ শুনতে যাব— তোমারও যাওয়া অত্যন্ত উচিত- এমন সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যায়।’ আবার সেদিনের চিঠিতেই লিখেছেন, ১১ মাঘের আবর্ত্তের মধ্যে অহোরাত্র ঘূর্ণিত। তুমি এসে দেখা না করলে আমার পক্ষে নড়া বড় কঠিন। কবে দেখা হবে?
রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মহ্মসমাজ পরবর্তীকালে নানা মতভেদের কারণে তিনটি পৃথক সমাজে (আদি, সাধারণ আর নববিধান) বিভিক্ত হয়ে পড়েছিল। বিক্ষিপ্ত সমাজ তিনটিকে একত্রিত করে ব্রাহ্মধর্ম তথা ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি (৯ মাঘ ১২৯১) জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে একটি ব্রাহ্মসম্মিলনের আয়োজন করেছিলেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলন সবকটি সমাজের প্রতিনিধিদের। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’ আর ‘পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান’ গান দুটি রচনা করেছেন। এছাড়াও ছিল সেবছরের মাঘোৎসবের জন্য গান রচনার তাড়া। এইসব কারণে সঙ্গ-পিপাসু রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন, ‘তার পরে ১১ই মাঘ— সেদিন দু বেলা নিমন্ত্রণ— সেদিন সকালে যদি ধরা দেও ত সমস্ত দিন ধরে রাখব। ইতিমধ্যে আর-একটা কারখানা আছে– তিন সমাজের একত্র উপাসনা হবে— ৯ই মাঘ অর্থাৎ কাল প্রাতে অত্রভবনে তিন সমাজের মহারথীরা একত্র হবেন। আপনি এলে – আপনি বলচি – তুমি এলে বড় আনন্দ হয়।’
আগামী সংখ্যায়
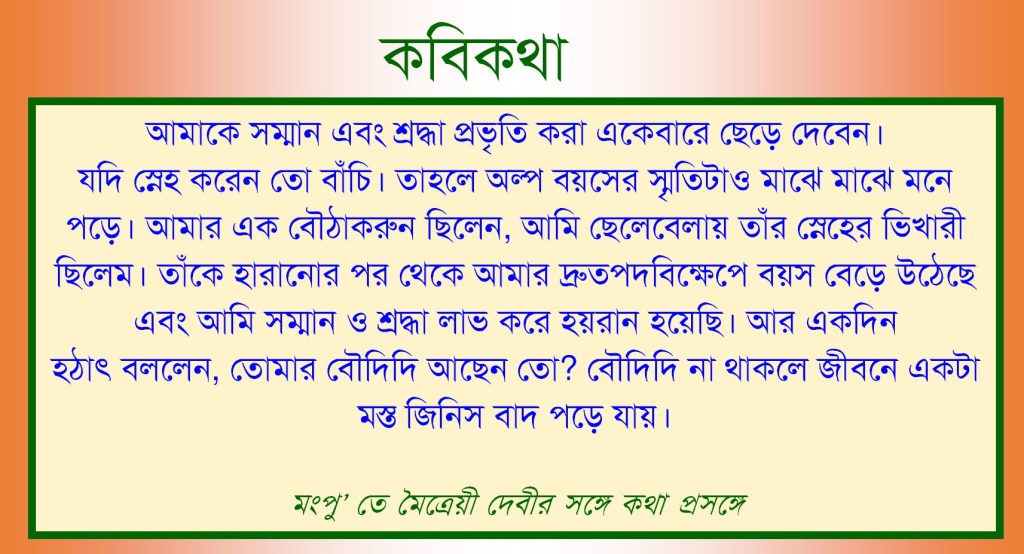

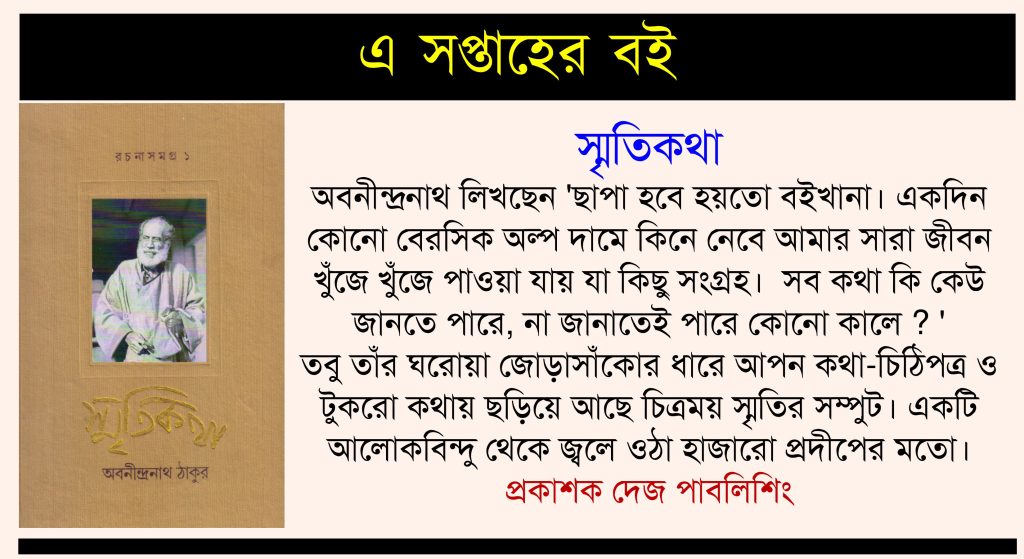
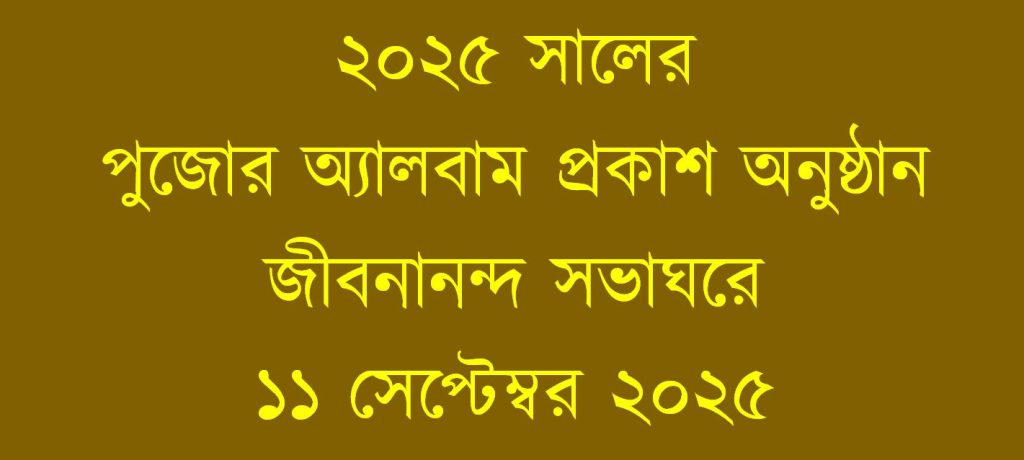







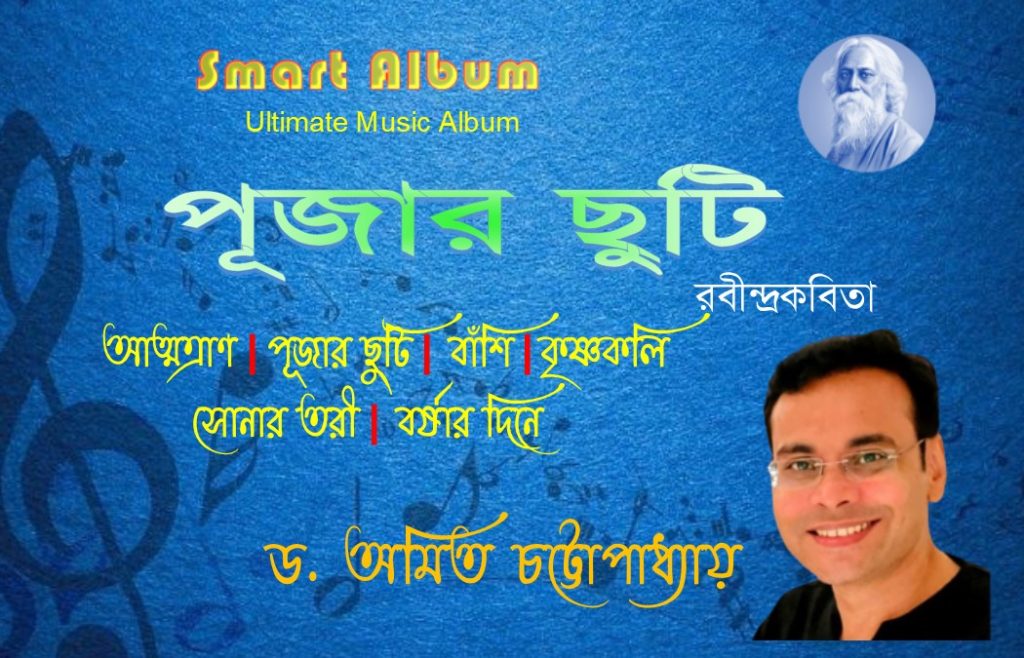
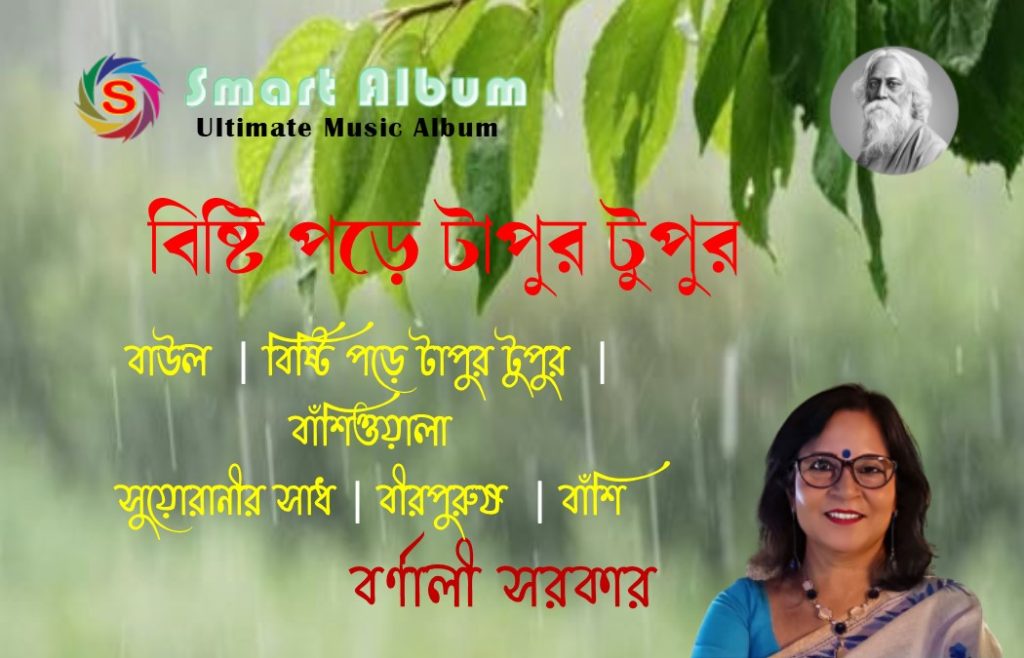
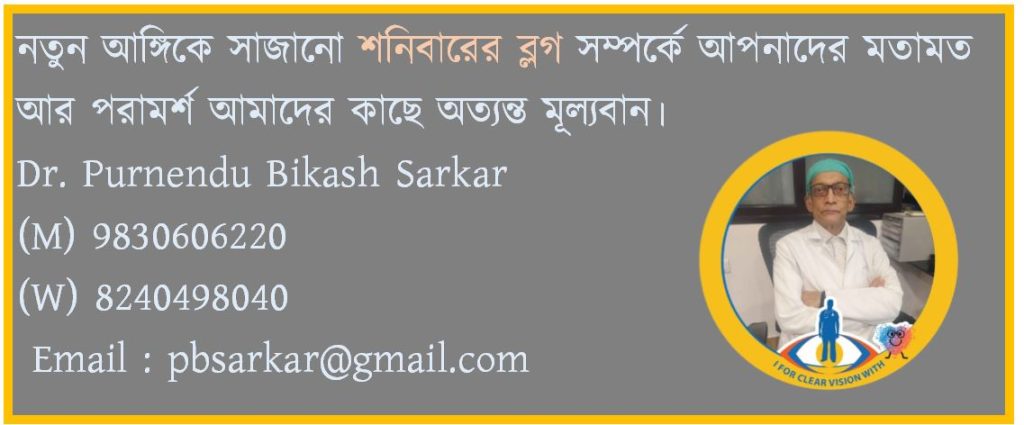
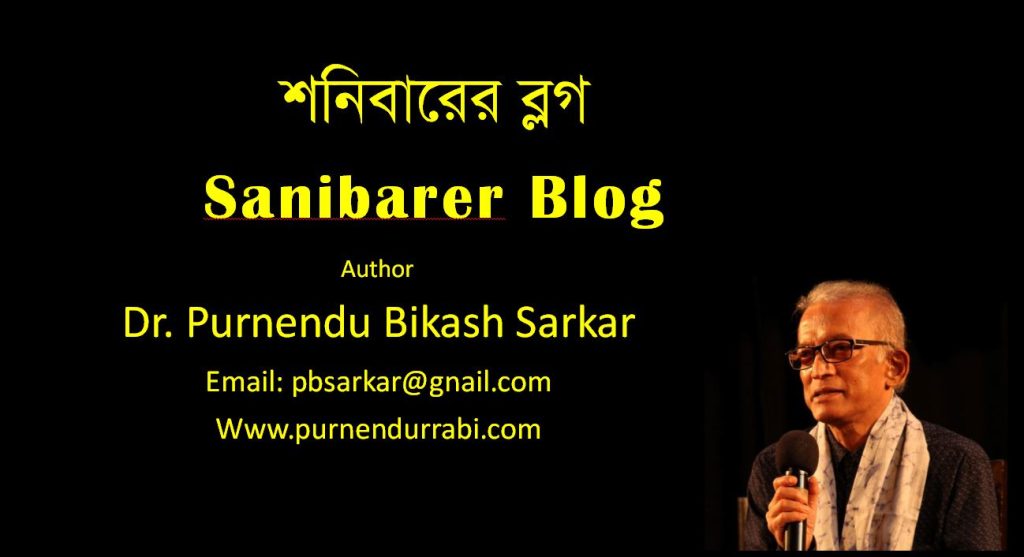

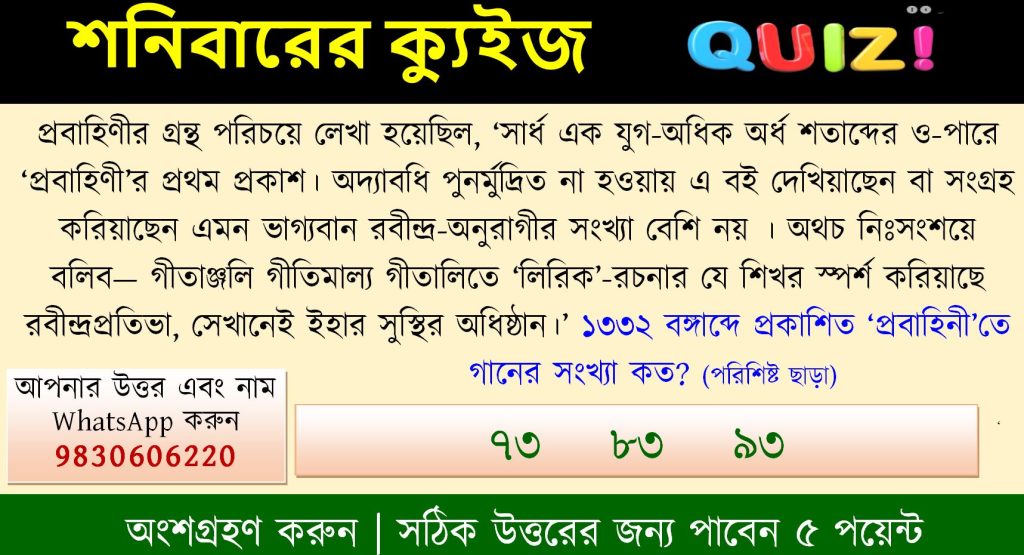
কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানতে হবে। তাঁকে সেরকমভাবে কজন আর জানতে পারি! তবু আপনি এই বিষয়ে সাহায্য করছেন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ন ঘটনা এবং ব্যক্তি দেরকে সংক্ষেপে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সারাটি সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকি এই শনিবারের ব্লগটির জন্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কতদিক দিয়ে আমাদের প্রিয় কবিকে আপনি প্রকাশ করছেন।