


পঞ্চম পর্ব
১২৯২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ মাসাধিককাল সোলাপুরে বাস করেছেন। সোলাপুরে এসে, কলকাতার ইট-কাঠ-চুন-সুরকির বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, ‘এখানে এসে অব্ধি এমনি ছুটির হাঙ্গামে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে । এখেনে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস—সমস্ত দিন একটা গড়িমসি ভাব—কখন লিখি বল ?… এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। এক্টা মহত্ত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্চে । মনে হচ্চে আমি নিষ্ফল । কি করব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে একটা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে।’
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তরের এর কাছাকাছি। বরাবরই তিনি গোয়া সমুদ্র উপকূলের বন্দোরা শহরে থাকতে ভালবাসতেন। সেখানকার শান্ত, নির্জন পরিবেশে, উদার প্রকৃতির পটভূমিকায় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আরাধ্য পরমেশ্বরকে। কিন্তু ১২৯৩ বঙ্গাব্দে আকস্মিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে চুঁচুড়ায় ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর অসুখের সময় উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে থেকেছেন। সেবা শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু চুঁচুড়ায় ফিরবার সময় মহর্ষিকে সঙ্গ না দিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন নাসিকে, সত্যেন্দ্রনাথের সরকারি বাসভবনে। ঋষিতুল্য পিতা দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শ তাঁর জীবনে যে কী বিপুল প্রভাব ফেলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেকথা তাঁর প্রিয়বন্ধুকে অকপটে জানিয়েছেন। নাসিকে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি কেটেছে আলস্যবিজড়িত ছুটির মেজাজে। আমরা বারবার দেখেছি একটানা ছুটি উপভোগ রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্টে কোনোও দিনই ছিলনা। কলকাতা কিংবা শান্তিনিকেতন, যখনই ছুটির সম্ভাবনা দেখা দিত, নানা কাজ-অকাজের ভিড়ে সে পালাবার পথ পেত না।
না, নাসিকে তেমন বিভ্রাট ঘটেনি। কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য ‘পড়ে-পাওয়া-চোদ্দআনা’র মত সেই ছুটিটাও নিরুপদ্রব হতে পারেনি। সে সময় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আয় বলে কিছুই ছিল না। জোড়াসাঁকোর জমিদারি থেকে মাসে দেড়শ-দুশো টাকার ভাতাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ, আপ্যায়ন, এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি ইত্যাদি জন্য টাকা জোগাড় করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। একবার ভেবেছিলেন নিজের পুরোনো বইগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা যদি পাওয়া যায়। কিন্তু সে পথে না গিয়ে আত্মীয়দের কাছ থেকেই চেয়ে-চিন্তে কাজ চালাতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও সামাল দিতে না পেরে প্রিয়নাথকে লিখেছেন, ‘অল্প টাকা হাতে পেয়েছিলুম কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ধার শুধুতে উড়ে গেছে। প্রতিদিনের খুচরো খরচ প্রায় ধার করে চালাতে হয়। জমিদারী থেকে এবারে অল্প টাকা এসেছে– আর দশ পনেরো দিনে বাকি টাকা আসার কথা আছে। যা হোক আমি দ্বিপুর কাছে ঐ তিনশ টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখব যদি পাওয়া যায়।’ সেই সঙ্গে ছিল আরও পঞ্চাশ টাকা বন্দোরার ঠিকানায় পাঠাবার আর্জি। এরপর থেকে বহুবার নানা প্রয়োজনে টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে হাত পাততে হয়েছিল প্রিয়নাথের কাছে, তা নতুন বই, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাংসারিক জিনিসপত্র কেনা, ব্যবসা, মেয়ের বিয়ে, ইত্যাদি যাইই হোক না কেন। প্রিয়নাথও সাধ্যমত রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করে গিয়েছেন।
ক্রমশঃ




পনেরো-কুড়ি বছর আগে, পুজোর সময় প্রকাশিত হত শিল্পীদের গান-কবিতার অ্যালবাম। আমরা অধীর হয়ে থাকতাম সেগুলি সংগ্রহ করবার জন্য। আজ, সেই দিনগুলি শুধুই স্মৃতি।
কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরে ঘুরে আসে। প্রযুক্তির হাত ধরে, এবারের পুজোয় আবার প্রকাশিত হবে দুটো রবীন্দ্রকবিতার অ্যালবাম। একেবারে ফিজিক্যাল। আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সামান্য দামে। যখন ইচ্ছা, আপনার স্মার্টফোনে উপভোগ করতে পারবেন সেই অ্যালবামের গান-কবিতা। আপনার টেবিলের একধারে আবার গড়ে উঠবে ‘অ্যালবাম লাইব্রেরি’। ফিরে আসবে পুরোনো নস্টালজিয়া।

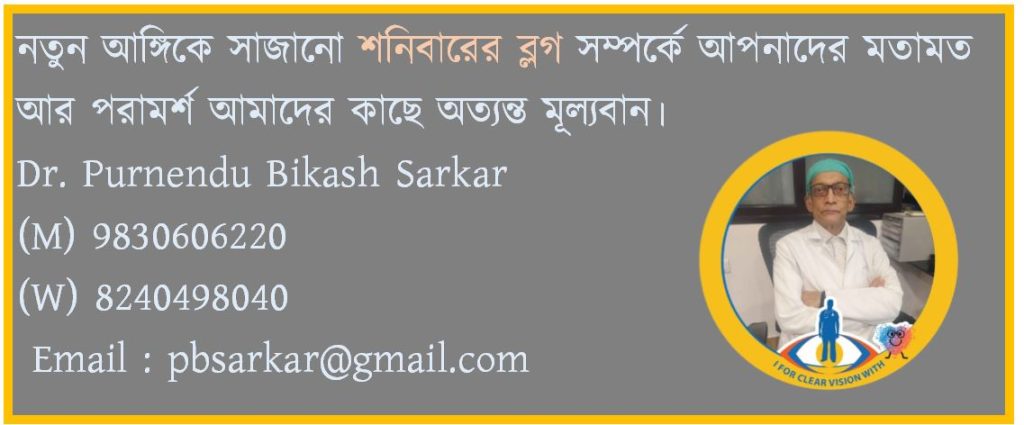
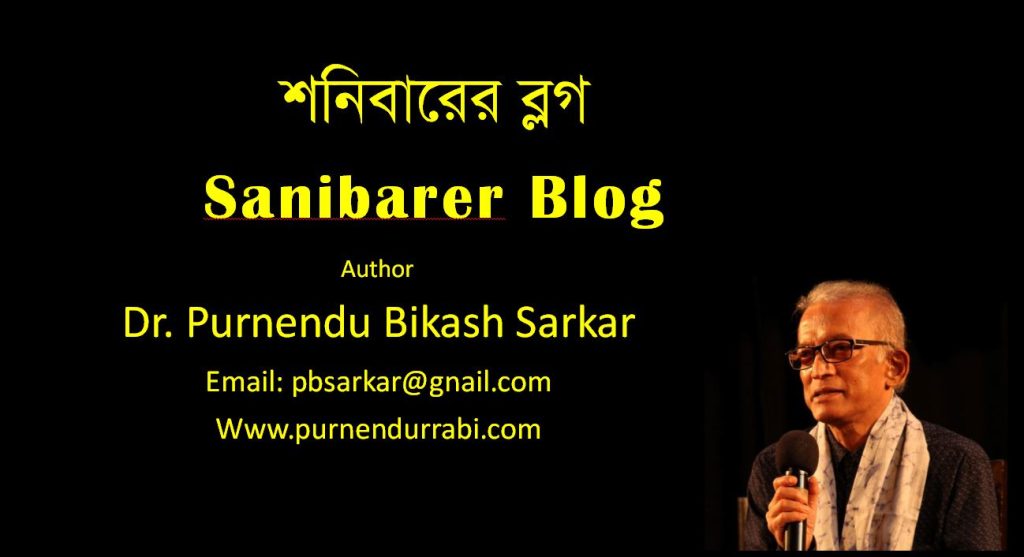
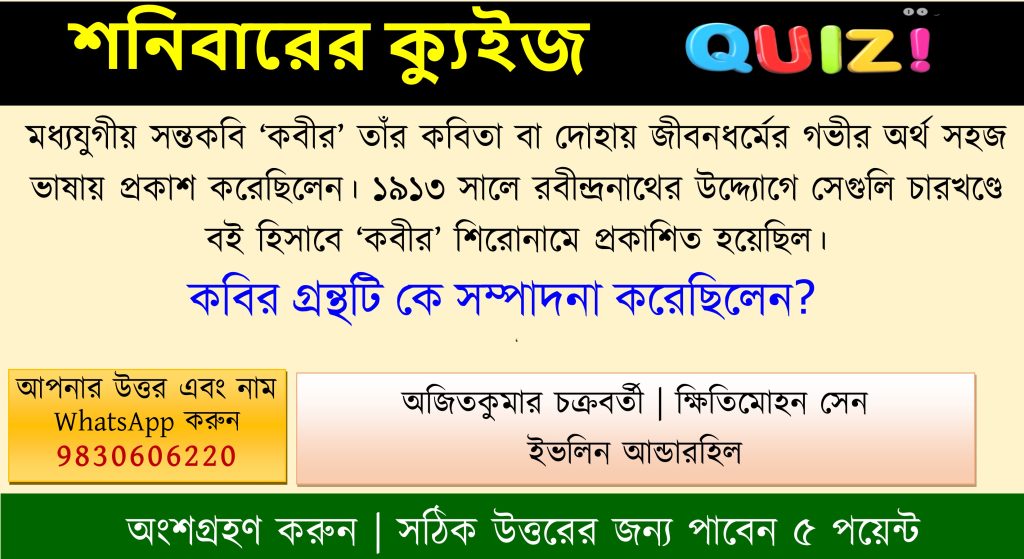

কবীর গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।
এ প্রসঙ্গে এবারের ব্লগের কুইজে আপনি আরো দুজনের নামের উল্লেখ করেছেন বলে ধন্যবাদ।
Songs of Kabir বা 100 poems of Kabir বইটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদিত । ওই বইটির কবিতাগুলি বেশীরভাগই ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকে, তবে কয়েকটি আবার অজিতকুমার চক্রবর্তির থেকে পাওয়া। আর ইভলিন আন্ডারহিল কবিতাগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করতে কবিকে সাহায্য করেছিলেন।
‘কবীর’ সম্পাদনা করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়।
এখন শনিবারের ব্লগের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। আমার প্রিয় কবির বিষয়ে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারি। যেটুকু জানি সেটা আবার নতুন করে জানি। এই জানার শেষ নেই আমার। আপনাকে পেয়েছি পাশে এটা আমার সৌভাগ্য বলেই মনে করি।